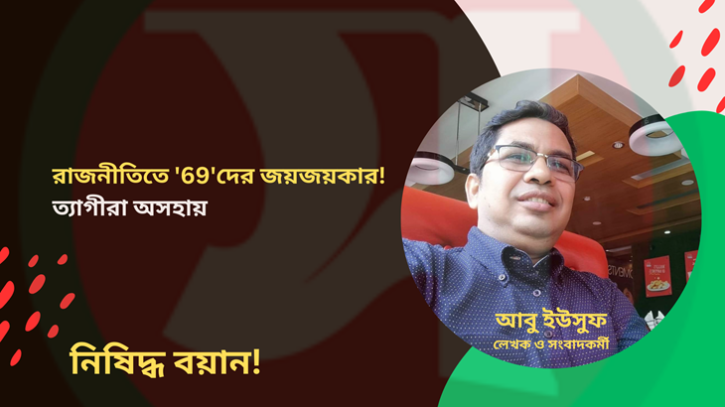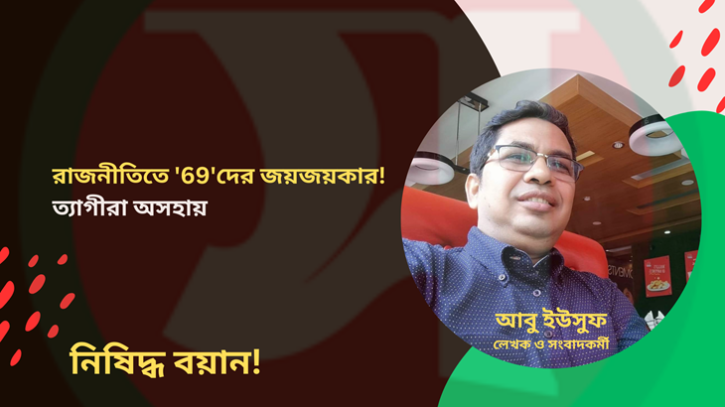
ওয়ার্ল্ড ক্রাইম নিউজ ২৪.কম (ভিডিও),লেখক ও সংবাদকর্মী আবু ইউসুফ,বৃহস্পতিবার ০২ অক্টোবর ২০২৫ || আশ্বিন ১৭ ১৪৩২ :
বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গন দিন দিন আরও অস্থির, আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলীয় রাজনীতিতে এক অদ্ভুত প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—যেখানে ত্যাগী, নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা ক্রমশ অবহেলিত, আর সুবিধাবাদীরা দিন দিন প্রভাবশালী হয়ে উঠছে। এদের নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন শব্দও তৈরি হয়েছে—‘৬৯’রা। সংখ্যাটির সঙ্গে সরাসরি কোনো বছরের বা আন্দোলনের সম্পর্ক নেই। বরং এটি রূপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে এক শ্রেণির ‘ক্যামেলিয়ন’ রাজনীতিকদের বোঝাতে—যারা পরিস্থিতি বুঝে রং বদলাতে সিদ্ধহস্ত।
আজ যারা ক্ষমতায়, কাল তারা বিরোধী দলে, আবার পরশু অন্য কোনো দলে; সুযোগ পেলেই জোটের ভেতর ঢুকে পড়তে এদের দ্বিধা নেই। এরা রাজনীতির এক অদ্ভুত বাস্তবতা তৈরি করেছে—যেখানে ত্যাগ, আদর্শ, সংগ্রাম বা দলীয় শৃঙ্খলা আর মুখ্য নয়, বরং কে কতটা সুবিধা নিতে পারে সেটাই হয়ে উঠেছে রাজনীতির মাপকাঠি।
Advertisement
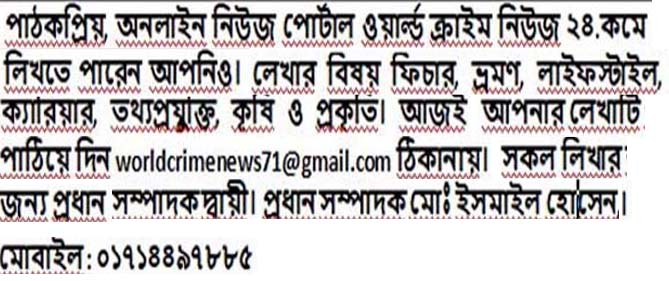
‘৬৯’দের উত্থান: দল বদলের সংস্কৃতি
বাংলাদেশের রাজনীতিতে দল বদল নতুন কোনো বিষয় নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই এর প্রভাব আমরা দেখেছি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এটি একেবারেই নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি—সব দলে, এমনকি ছোট দলগুলিতেও এক শ্রেণির নেতা আছেন যারা সব সময় সুযোগসন্ধানী। তাদের মূল লক্ষ্য দল নয়, বরং ব্যক্তিগত অবস্থান, ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করা।
বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার জটিলতা ও ক্ষমতায় যাওয়ার প্রবল প্রতিযোগিতাই এই ‘দল বদলের ডিগবাজী’র মূল চালিকাশক্তি। ২০০৮ সালের পর থেকে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কারণে ক্ষমতাসীন দলে ঠাঁই নেয়া ছিলো অনেকের টিকে থাকার একমাত্র পথ। অন্যদিকে, বিরোধী দলে সক্রিয় থেকেও অনেকে গোপনে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করেছেন। এ দ্বিমুখী খেলাই মূলত রাজনীতিকে করেছে দুর্বল ও আদর্শহীন।
দলবদলের সংস্কৃতি: ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশের রাজনীতি শুরু থেকেই আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রামী চরিত্রে গড়ে উঠেছিলো। পাকিস্তান আমলে স্বাধিকার আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন কিংবা মুক্তিযুদ্ধ—সব ক্ষেত্রেই নেতৃত্বে ছিলেন ত্যাগী মানুষ। কিন্তু স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ৭৫ পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসন, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এবং বারবার রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে একটি অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা তৈরি হয়—দলবদল।

যে রাজনীতিকরা একসময় নিজেদের একটি দলের আদর্শিক সৈনিক হিসেবে পরিচয় দিতেন, পরবর্তীতে ক্ষমতার লোভ বা ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রতিপক্ষ দলে যোগ দিয়েছেন। এ সংস্কৃতি এখন এতটাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে যে, নির্বাচন এলে ‘দলবদলের হাট’ বসে যায়। ক্ষমতাসীনদের দলে যোগ দিলে পদ-পদবি, সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবসায়িক নিরাপত্তা মিলবে—এ ধারণাই এখন বাস্তবতা।
‘৬৯’দের উত্থান: সুবিধাবাদের প্রতীক
‘৬৯’রা আসলে কারা? এরা মূলত সেই শ্রেণির রাজনীতিবিদ, যারা কোনো আদর্শে বিশ্বাসী নন। একদিন বিরোধী দলে থাকেন, পরদিন ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সেলফি তোলেন। একসময় গণতন্ত্র, অধিকার ও সংগ্রামের বুলি আওড়ান, আর ক্ষমতা এলে একই ব্যক্তি আবার দমননীতির সহযোগী হয়ে যান।
এ শ্রেণির উত্থানের পেছনে কয়েকটি কারণ স্পষ্ট—
- দলীয় নেতৃত্বের দুর্বলতা – দলগুলো প্রায়ই যোগ্যতা ও ত্যাগের বদলে সুবিধাবাদী ও চাটুকারদের অগ্রাধিকার দেয়।
- আদর্শহীন রাজনীতি – গণতন্ত্রের চর্চা দুর্বল হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলো মূলত ক্ষমতাকেন্দ্রিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে।
- অর্থনৈতিক সুবিধা – ব্যবসা-বাণিজ্য, টেন্ডার, কমিশন ও রক্ষাকবচ পাওয়ার জন্য রাজনীতির ব্যবহার ক্রমেই বেড়েছে।
- রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা – ক্ষমতার পালাবদলের ভয় বা আশায় অনেকেই আগেভাগে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।
ফলাফল হচ্ছে—আজকের রাজনীতিতে প্রকৃত ত্যাগীরা পদবঞ্চিত, প্রান্তিক ও অবহেলিত; আর ‘৬৯’রা ক্ষমতায় থেকে ভোগবিলাসে মগ্ন।
Advertisement
প্রতিটি উপজেলায় সংবাদদাতা আবশ্যক। যোগাযোগ ০১৭১৪৪৯৭৮৮৫

ত্যাগী নেতাকর্মীদের অসহায়ত্ব
রাজনীতির মেরুদণ্ড হলো মাঠপর্যায়ের ত্যাগী কর্মীরা। কিন্তু তাদের বাস্তবতা আজ ভিন্ন। একসময় যারা রাস্তায় আন্দোলন করেছেন, লাঠিচার্জ, মামলা-মোকদ্দমা সহ্য করেছেন, জেল খেটেছেন—তাদের এখন প্রাপ্য সম্মান নেই। তাদের অনেকেই এখনও মাঠে সক্রিয়, কিন্তু দলীয় নেতৃত্ব তাদের ভুলে গেছে।
মনোনয়ন বণ্টনের সময়ও তাদের নাম আসে না। বরং, যারা হঠাৎ এসে যোগ দিয়েছে বা যাদের কাছে অর্থবিত্ত আছে, তারাই টিকিট পেয়ে যায়। এতে দলের ভেতর ক্ষোভ ও হতাশা বাড়ছে। এক সময়ের ত্যাগী নেতারা অনেকটা নিরাশ হয়ে মাঠ ছাড়ছেন। তাদের সন্তানরাও রাজনীতির প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। ফলে রাজনীতির ভেতর থেকে আদর্শিক ধারাটা ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।
দলের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো এখন তাদের হাতে নেই; বরং ‘৬৯’রা রাতারাতি নেতা হয়ে তাদের ওপর বসে যাচ্ছেন। যারা বছরের পর বছর কষ্ট করে সংগঠন চালিয়েছেন, তারাই এখন কর্মসূচির বাইরে, সিদ্ধান্তগ্রহণের বাইরে, এমনকি প্রায়ই উপেক্ষিত।
অন্যদিকে, যখন সুবিধাবাদী ‘৬৯’রা পদ-পদবি নিয়ে বিত্ত-বৈভব গড়ে তুলছেন, তখন ত্যাগীরা পরিবার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। এ অবহেলা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক কর্মীদের আস্থা ও প্রেরণাকে ক্ষয় করছে।
সুবিধাবাদীদের শক্তি: অর্থ, পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রভাব
‘৬৯’রা রাজনীতিতে এতটা প্রভাবশালী হতে পেরেছে মূলত তিন কারণে।
- অর্থনৈতিক প্রভাব – বর্তমান রাজনীতিতে টাকা ছাড়া কিছুই চলে না। নির্বাচনী খরচ, প্রচারণা, দলীয় তহবিল—সব জায়গায়ই টাকা দরকার। যাদের কাছে অর্থ আছে, তারা সহজেই দলের শীর্ষ পর্যায়ে জায়গা করে নিতে পারে।
- পৃষ্ঠপোষকতা – অনেক সময় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন মহলের আশীর্বাদ থাকে এ সুবিধাবাদীদের ওপর। এর ফলে দলীয় কাঠামো উপেক্ষা করেও তারা অল্প সময়ে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।
- গণমাধ্যম ও প্রচারণা – অর্থ ও প্রভাবের কারণে এরা নিজেদের সাফল্যের গল্প প্রচার করতে পারে। ফলে সাধারণ কর্মীর চোখে তারা ‘নেতা’ হয়ে ওঠে, যদিও তাদের কোনো আন্দোলন বা ত্যাগের ইতিহাস নেই।
দলগুলোর দ্বিমুখী সংকট
বাংলাদেশের প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আজ একই ধরনের সংকটে পড়েছে।
- আওয়ামী লীগে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারণে স্বার্থান্বেষী মহল দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে। আওয়ামী লীগের অনেক প্রবীণ ও ত্যাগী নেতারাই আক্ষেপ করে বলেন, আন্দোলনের দিনগুলোতে যারা মাঠে ছিলেন না, তারাই হয়েছেন মন্ত্রী-এমপি।
- বিএনপির ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা। দমনপীড়নের সময় যারা কারাভোগ করেছেন বা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন, তাদের অনেকেই অবহেলিত। বরং অনেক জায়গায় দেখা গেছে, হঠাৎ ‘দল পরিবর্তন’ করে আসা নেতারাই পদ পেয়েছেন।
এ প্রবণতা রাজনৈতিক দলগুলোকে ভেতর থেকে খালি করে দিচ্ছে। ত্যাগী কর্মীরা যদি দল থেকে আস্থা হারান, তবে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো রূপ নেবে কেবল প্রভাবশালীদের ‘ক্লাবে’।
গণতন্ত্র ও নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়
রাজনীতিতে আদর্শহীনতা গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। যখন সুবিধাবাদীরা দখল নেয়, তখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে ক্ষমতায় টিকে থাকা। এতে একদিকে প্রশাসনিক দুর্নীতি বেড়ে যায়, অন্যদিকে জনগণের সঙ্গে দলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। জনগণও রাজনীতির প্রতি আস্থা হারায়।
একসময় এ দেশের মানুষ রাজনীতিকে দেখত ‘আদর্শের লড়াই’ হিসেবে। আজ সেটি পরিণত হয়েছে ‘সুবিধার লড়াই’-এ। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে গণতন্ত্র কেবল কাগজে-কলমে থাকবে, বাস্তবে তা হবে ক্ষমতাসীনদের দখলদারিত্বের নামান্তর।
এতে নেতৃত্বের মান কমে যায়। সুযোগসন্ধানীরা ক্ষমতায় গিয়ে দেশ চালালে রাষ্ট্রনীতি অগভীর ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলত, রাজনীতি হয়ে দাঁড়ায় কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের মঞ্চ, যেখানে জনগণের স্বার্থ গৌণ।
গণতন্ত্রের জন্য হুমকি
‘৬৯’দের দাপট শুধু দলীয় রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং গণতন্ত্রের জন্যও মারাত্মক। কারণ গণতন্ত্র টিকে থাকে আদর্শ, নীতি ও জনআস্থার ওপর। কিন্তু যখন জনগণ দেখে—একই ব্যক্তি একদিন গণতন্ত্রের নাম করে আন্দোলন করেন, আরেকদিন স্বৈরতন্ত্রের পাশে দাঁড়ান—তখন তারা রাজনীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।
এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য একটি গুরুতর হুমকি। কারণ, জনগণ যদি রাজনীতিকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে, তবে তাদের চোখে গণতন্ত্রও অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। তখন সামাজিক অস্থিরতা, চরম হতাশা ও বিকল্প চরমপন্থার উত্থান ঘটে।
জনগণের অসন্তোষ ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ
সুবিধাবাদী রাজনীতির ফলে সাধারণ মানুষও রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ভোটের মাঠে অংশগ্রহণ কমছে, ভোটাররা আগ্রহ হারাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মানুষের অবিশ্বাস বেড়েছে। যদি এ প্রবণতা অব্যাহত থাকে, তবে আগামী দিনে আরও বড় রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হবে।
এ শূন্যতার সুযোগ নেবে চক্রবৃত্তিক রাজনৈতিক শক্তি, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবে। ফলে দেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্র আরও বেশি ঝুঁকির মুখে পড়বে।
করণীয়: কিভাবে ‘৬৯’দের রুখে দাঁড়ানো সম্ভব?
বাংলাদেশের রাজনীতিকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে ‘৬৯’দের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি। এর জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে—
- দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা – নেতৃত্ব নির্বাচনে ত্যাগ, যোগ্যতা ও কর্মীর মতামতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ত্যাগীদের মূল্যায়ন – যারা সংগ্রামে সামনে থেকেছেন, তাদের পদ-পদবি ও সিদ্ধান্তগ্রহণে জায়গা দিতে হবে।
- নৈতিক রাজনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা – আদর্শভিত্তিক রাজনীতি চর্চা না করলে দলগুলো শুধু ভোগবাদী গোষ্ঠীতে পরিণত হবে।
- আইনি সংস্কার – দলবদল রোধে আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নির্বাচনের আগে ‘দলবদলের হাট’ বন্ধে কার্যকর বিধান প্রয়োজন।
- জনগণের চাপ – জনগণকেও ভোটের মাধ্যমে সুবিধাবাদীদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে, যাতে ত্যাগীদের জন্য পথ তৈরি হয়।
বাংলাদেশের রাজনীতির আজকের বাস্তবতা হলো—‘৬৯’দের জয়জয়কার, আর প্রকৃত ত্যাগী নেতাকর্মীদের অসহায়ত্ব। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আরও ভঙ্গুর হয়ে যাবে। তখন গণতন্ত্র কেবল কাগজে-কলমে থাকবে, আর বাস্তবে ক্ষমতা কেবল সুবিধাবাদীদের হাতেই ঘুরপাক খাবে।
তবে আশা আছে। যদি রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা নেয়, ত্যাগী কর্মীদের মর্যাদা দেয় এবং আদর্শভিত্তিক রাজনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে, তবে পরিস্থিতি বদলাতে পারে। নইলে ‘৬৯’দের হাতেই রাজনীতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যন্ত সবকিছু জিম্মি হয়ে যাবে।
Advertisement
গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজন—ত্যাগী নেতাকর্মীদের নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনা, এবং সুবিধাবাদীদের প্রবাহ রোধ করা। অন্যথায় বাংলাদেশে রাজনীতি চিরকাল ‘দলবদলের বাজার’ হিসেবেই পরিচিত হয়ে থাকবে, যেখানে ‘৬৯’রা হাসবে, আর ত্যাগীরা কাঁদবেন।